বাতায়ন/শারদ/অন্য চোখে/৩য় বর্ষ/২২তম সংখ্যা/১লা আশ্বিন, ১৪৩২
শারদ | অন্য চোখে
তপোময় ঘোষ
কাঁচা
আলকাতরার গন্ধ
"দুর্গোৎসবের আরও একটা অনুষঙ্গ মনে আছে। আমাদের মামারা ভাগচাষি ছিলেন, গ্রামে ভচ্চাযদের জমি ভাগে চাষ করতেন। মনে আছে মেজোমামা মাঠের চৌধুরী-পুকুর থেকে পুজোর জন্য পদ্মফুল, কুঁড়ি আর ভোজের জন্য পদ্মপাতা তুলে এনে ভচ্চাযদের বাড়িতে দিত।"
না, শত-শত বছর আগের কথা নয়, এমনকি একশো বছর আগের কথাও নয়। মাত্র চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগের মানে গত শতকের ষাট-সত্তরের দশকের, আমাদের শৈশব-কৈশোরের ভাদ্র-আশ্বিন মাস শরৎকাল বা শারদোৎসব বা দুর্গাপূজার কথা।
তখনও এদেশের বুকে সবুজ বিপ্লব
বা খাদ্যে স্বয়ংম্ভরতা আসেনি। নিতান্ত দেশিয় গতানুগতিক বা ট্র্যাডিশনাল আমন ধান বছরে একবার আষাঢ়-শ্রাবণের বর্ষার জলে রোপন করে দীর্ঘ ছমাস পরে সেই অঘ্রান-পৌষে কাটা হত। ফলন হত বিঘা প্রতি সাত-আট মন, বড়জোর দশ মন। নিতান্ত জমিদার-জোতদার
বা অনেক বেশি জমির মালিক ছাড়া সব মাঝারি, ক্ষুদ্র প্রান্তিক কৃষকের এবং গ্রামের অন্যান্য বৃত্তিজীবী
মানুষ ও যারা গ্রামীণ
কৃষিজীবী গৃহস্থ পরিবারের মানুষ, তাদের প্রায় সকলেরই
পৌষের সেই গোলাজাত ধান কারও বৈশাখে, কারও জ্যৈষ্ঠ মাসে
কারও আষাঢ়-শ্রাবণ মাস অবধি চলত।
অঘ্রান থেকে ঘরের ধানের চালের ভাত-মুড়ি খাওয়া হত। ভাদ্র মাসেই শুরু হত সর্বাত্মক
এবং সর্বনাশা অভাব। অভাব চালের,
মুড়ির, চিঁড়ে, খই বা পাকা তাল
কুড়িয়ে বড়া বানানোর চাল-গুঁড়িরও। গোয়ালে বাঁধা গোরু-মোষের খড়ের
অভাব। ফলত গাঁয়ের গেরস্ত চাষিদের বাড়িতে হাঁড়ি না চড়ার
অবস্থা। আর তার মধ্যেই চলে আসত আশ্বিন মাস, দুর্গোৎসব।
আমাদের মাঝারি গ্ৰাম বর্ধমানের (অধুনা পূর্ব বর্ধমান) কেতুগ্রামের শিবলুন গ্রামে
ছয়-সাতখানা দুর্গাপুজো হলেও তার মধ্যে
সব পাঁচ-ছটাই ব্রাহ্মণ জমিদার তথা
তাদের আত্মীয়-স্বজন মুখুজ্জে-চাটুজ্জেদের। চাষাদের জন্য ছিল
বাগদিদের সঙ্গে ভাদ্র সংক্রান্তিতে
মনসা পূজোর তোড়জোড়। গাঁয়ের চাষারাও খরিস, কেউটে সাপ ধরে
তা নাচিয়ে মনসামঙ্গলের কাহিনি মতে বেহুলার ভাসানের গান
গাইত। আমাদের মতো নিম্নবিত্ত চাষাদের বাড়িতে দুর্গাপুজোর কোন প্রভাব পড়ত না।
যেটুকু পড়ত তা হল রাঙামাটি সংগ্রহ করে এনে তা বালতির জলে গুলে মাটির দেওয়াল-মেঝে পরিপাটি করে নিকানো। তারপর শুকালে মুদিখানার দোকান থেকে চার আনার
খড়ি কিনে এনে দেয়ালে আলপনা আঁকা, লক্ষ্মীর পদচিহ্ন প্যাঁচা
ইত্যাদি।
আর প্রচলন ছিল, ওই মুদির
দোকান থেকেই মাটির ভাঁড়ে আলকাতরা কিনে এনে কাঠের দরজা-জানালায়
লেপে দেওয়া। আলকাতরার লেপন দিলে ঘুনসহ অন্যান্য পোকামাকড়
দূরে থাকত। এছাড়া বড়লোক বা পাকা ঘরের মালিকরা তাদের দেওয়াল প্লাস্টার করার সময়
যেমন মেঝে থেকে অন্তত দু'ফুট উঁচু পর্যন্ত নেট
সিমেন্ট করত। তার অনুকরণে মাটির ঘরের মালিক গরিবগুবরোরাও তাদের মাটির দেওয়ালের ওই
দু'ফুট পর্যন্ত আলকাতরা দিয়ে রং
করত। পাড়াগাঁয়ের সব বাড়িই তখন যেহেতু কাঁচা এবং মাটির তাই সব বাড়ির আলকাতরার রংয়ের গন্ধে ম-ম। এই গন্ধেই আমাদের পুজো আসত। এখনও কাঁচা আলকাতরার গন্ধ পেলে শৈশবের পুজোর স্মৃতি জ্যান্ত হয়ে মনে নড়েচড়ে
ওঠে। এছাড়া দারিদ্র্যের মধ্যে পালাপার্বণের স্মৃতিতে আছে পুজোর বাজার মানে
কোনক্রমে একটা নারকেল চার-পাঁচ টাকায় কিনে তা কুড়ে নাড়ু
বানানো। আর চালে হলুদ মাখিয়ে চাল ভাজা। তাতে কিছু কুসুমের সুগন্ধি বীজ মেশানো। পুজোর ক'দিন ছোট-ছোট মেয়েরা
তাদের ফ্রকের কোঁচড়ে নিয়ে ঘুরে ঘুরে খেত। আমরা অবশ্য ফ্রকের
বদলে গলায় বেঁধে দেওয়া গামছার কোঁচড়ে নিয়ে খেতাম।
দুর্গোৎসবের আরও একটা অনুষঙ্গ
মনে আছে। আমাদের মামারা ভাগচাষি ছিলেন, গ্রামে ভচ্চাযদের জমি ভাগে চাষ করতেন। মনে আছে মেজোমামা
মাঠের চৌধুরী-পুকুর থেকে পুজোর জন্য পদ্মফুল, কুঁড়ি আর ভোজের জন্য পদ্মপাতা তুলে এনে ভচ্চাযদের বাড়িতে দিত। মামা আমাদের ওই
দুর্গম পুকুরে সঙ্গে নিয়ে যেত। সে এক আনন্দের আখ্যান।
ভচ্চাযরা এইসব সেবার
প্রতিদানে নবমী পুজোর দিনে মায়ের প্রসাদ খেতে নিমন্ত্রণ দিতেন। মেজোমামার সঙ্গে
ভচ্চাযদের বাড়ির ভোজ খাওয়ার দুটি কথা মনে আছে। নবমীর দিনে ঠাকুর বাড়ির উঠোনে
কুয়োপাড়ের ধারে বসে ভোজ খাওয়া। গৌড় হাটুই আর পচা বাড়ুইয়ের পরিবেশন
করা। সেখানে তরকারি বলতে পই কচুর ঘ্যাঁট আর বলির চালকুমড়োর
তরকারি। সেই পই কচুর ঘ্যাঁটের স্বাদ যেন এখনও মুখে লেগে আছে।
সমাপ্ত
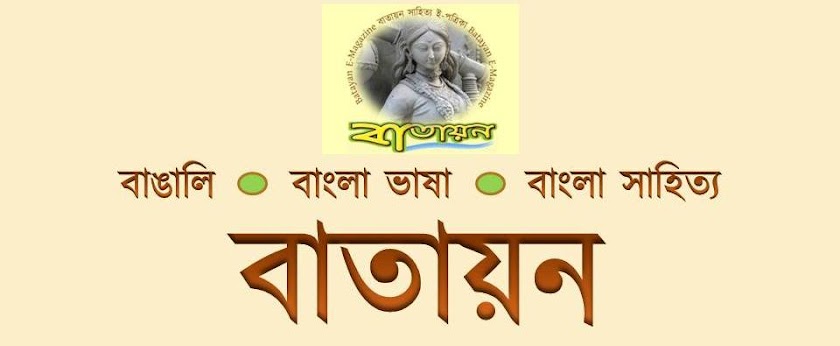












No comments:
Post a Comment