বাতায়ন/হাপিত্যেশ/যুগলবন্দি/২য়
বর্ষ/৫ম সংখ্যা/৩২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১
হাপিত্যেশ | যুগলবন্দি
বিবেক
"বিবেকানন্দ আপামর মানুষের বিবেক জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত পারলেন কি? তাঁর বলিদান কি শেষপর্যন্ত বেকার গেল না! মানুষের তাৎক্ষনিক সুখ, লোভ-লালসার কাছে হেরে গেলেন বিবেকানন্দ! নাকি মানুষ হেরে গেল এত বড়, মহান একজন ব্যক্তিকে পেয়েও তাঁকে, তাঁর উদ্দেশ্য কাজে লাগাতে না পেরে। হয়তো তাই আজকের এই দুদর্শা।"
ব্রাহ্মমুহূর্তে সূর্যের
প্রথম কিরণ বিবেকানন্দের পা ছুঁয়ে নিজের দৈনন্দিন কর্মে গেল। যেন বিবেকানন্দের পাদপদ্মস্পর্শে
নিজেকে ধন্য, পুণ্য করে, তাঁর তেজোদীপ্তিতে নিজের দীপ্তিমান প্রভা আরো উদ্দীপিত করে
সম্পন্ন করবে তার সমস্ত দিনের কর্ম। বিবেকানন্দ— মহাবীর্যবান সিদ্ধ জ্যোতিষ্ক।
বইয়ের তাকে রাখা বিবেকানন্দ,
বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন। মনে পড়ল কন্যাকুমারীর বিবেকানন্দ-শিলার কথা। চারিদিকে উত্তাল
সমুদ্র, তারই মধ্যে সাঁতরে গিয়ে বিবেকানন্দ ধ্যান করছেন। বিবেকানন্দের ধ্যানের মাধ্যমে
তাঁর গুরু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদেশ পেলেন।
প্রাগৈতিহাসিক যুগে
অশিক্ষিত, মূর্খ, বিজ্ঞান সম্পর্কে বিন্দুমাত্র জ্ঞানহীন মানুষ সূর্যসহ যে-কোনো অতিপ্রাকৃত
শক্তিকেই দেবতাজ্ঞানে পুজো করত। শিক্ষা, জ্ঞান, চেতনা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের
ধারণা, বিশ্বাসেরও বদল হওয়াই উচিত।
বিবেকানন্দ নিজে কট্টর
যুক্তিবাদী ছিলেন। তিনি কি আত্মত্যাগ করলেন না! নাকি তাঁর এই আত্মবলিদান, আধ্যাত্মবাদে
বিশ্বাসের পিছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল? তৎকালীন মেরুদণ্ডহীন পরাধীন ভারতবর্ষের পুর্ণগঠনের
জন্য এই আত্মবলিদান একান্তই জরুরি ছিল?
বিবেকানন্দ আপামর মানুষের
বিবেক জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত পারলেন কি? তাঁর বলিদান কি শেষপর্যন্ত বেকার
গেল না! মানুষের তাৎক্ষনিক সুখ, লোভ-লালসার কাছে হেরে গেলেন বিবেকানন্দ! নাকি মানুষ
হেরে গেল এত বড়, মহান একজন ব্যক্তিকে পেয়েও তাঁকে, তাঁর উদ্দেশ্য কাজে লাগাতে না পেরে।
হয়তো তাই আজকের এই দুদর্শা।
মানুষ এবং মনুষ্যেতর
প্রাণীর মধ্যে আশমান-জমিন ব্যবধান। সেই ব্যবধান কি বিবেকের কাছে পরাজিত হচ্ছে না? জীবিকা-নির্বিশেষে
তা কি ক্রমশ অবলুপ্তির পথে?
বিবেক বিসর্জনের মাধ্যমেই
কি এলিট সমাজে ঠাঁই পান আজকের মানুষ! সে তিনি ডাক্তার, শিক্ষক, সমাজসেবী যিনিই হোন-না-কেন।
আদর্শ একটি পেশায় নিযুক্ত কোন একজন মানুষ যদি যে-কোনো তাৎক্ষনিক লোভের কাছে পরাজিত
হয়ে মনুষ্যেতর প্রাণীর মতো আচরণ করতে শুরু করেন, তখন কপালে দীর্ঘ ভাঁজ পড়াই স্বাভাবিক।
সেইসঙ্গে আছে একজন মানুষের
সব পাওয়ার লোভ। একজন সাহিত্যিক যদি প্রয়োজনীয় শিক্ষা ছাড়া চিকিৎসা করতে যান তাহলে রোগীর
কী অবস্থা হতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না, তেমনই একজন ডাক্তার যদি প্রয়োজনীয় শিক্ষা,
চর্চা ছাড়া সাহিত্যিক হতে চান, অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এরপর রইল মেধা ও মননের প্রসঙ্গ।
শুধু টাকা থাকলে বই ছাপিয়ে প্রকাশ করলেই সাহিত্যিক হওয়া যায় না। সাহিত্যচর্চা অবশ্যই
ভাল তবে তার নিজের সচেতনতা বোধ এবং সমাজকে অনুভব করার মতো মন-মনন থাকা অত্যন্ত জরুরি।
এ-প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে, ‘ছাগল দিয়ে লাঙল চাষ হয় কি কখনো?’ সে সকাল বা সন্ধ্যায়
ব্যা-ব্যা-ই করবে কেবল।
যে-কোনো কাজের জন্য
দরকার প্রয়োজনীয় শিক্ষা, চর্চা, অধ্যাবসায়, নিষ্ঠা। নইলে অল্পশিক্ষিত, পুঁথিগত বিদ্যায়
অপারঙ্গম গ্রামের চাষাভুষো মানুষের কাছে শহুরে অহংকারী বিদ্বান সম্প্রদায়ও ডাহা ফেল
করতে বাধ্য।
মানুষ নিজের নিজের বিবেক
জাগ্রত করে বিবেকের দ্বারা চালিত হবে, নাকি ‘বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে’ কেঁদেই যাবে
চিরকাল!
বাতায়ন/হাপিত্যেশ/যুগলবন্দি/২য়
বর্ষ/৫ম সংখ্যা/৩২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১
হাপিত্যেশ | যুগলবন্দি
বিবেক
"কেউ পুঁথিগত বিদ্যায় পারদর্শী হচ্ছে অথবা মস্ত ডিগ্রিধারী হচ্ছে কিন্তু তার মাঝে মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়নি। তারাই নানা রকম অসমাজিক কর্মকাণ্ডে জারিত হচ্ছে । কেননা শুধুমাত্র একডেমিক শিক্ষা মানুষের মনুষ্যত্ব গড়নে ভূমিকা রাখতে পারে না। এই শিক্ষার উপরেও একজন শিক্ষক সবসময় সঠিক পথে দেখিয়ে চলেছে। তাকে স্বীকার না করে, তার অনুশীলন অস্বীকার করে তারা রিপু অনুগামী হয়েই থেকে গেছে। "
বিচিত্র মন বিচিত্র সমাজ, বিছিয়ে আছে ঈশ্বরের পথে। ভুল
অন্যায় অপরাধ প্রত্যেকের একজন শিক্ষক আছে। বিবেক। অস্বীকার করি তাকে। সে নিজের
দুয়ার খুলে রাখে সেখানেই ঈশ্বরের অভিগমন। তাকে যাচাই করি তাকে দিয়েই। অথচ সেই-ই
প্রকৃত শিক্ষা দিয়ে চলেছে অনবরত। আমরা মানুষ প্রজাতি, অন্যান্য প্রাণীকুলেরও আছে
বিবেক। যা কিছু সত্য বা মিথ্যা তার বিকল্প বেছে নিই নিজের মতো করে।
জন্মের সময় ছয়টি রিপু নিয়েই মানুষের জন্ম হয়। ছয়টি রিপুর তাড়না
মানুষের মাঝে তাই জন্মগতভাবেই থাকে। কাম (বস্তু কাম, যৌন কাম), ক্রোধ (রাগ), লোভ,
মদ (অহংকার), মোহ ও মাৎসর্য (হিংসা)। বয়বৃদ্ধি ও পারিপার্শ্বিক প্রভাবে এই ছয়টি
রিপুর বশবর্তী হয়ে আমরা পরিচালিত হই আমৃত্যু। এ ছয়টি রিপুর যে-কোনো এক বা একাধিক
রিপুতে আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়ে থাকে। কেউ কামাধিক, কেউ
ক্রোধাধিক, কেউ বা রাগাধিক ইত্যাদির হয়ে থাকে।
ছয়টি রিপু সমভাবে বিদ্যমান না হলেও কিন্তু পরিবেশ আর বিচারবোধ
ভিত্তিতে রিপুগুলোর প্রভাব বলবৎ হয়ে প্রকাশ পায়। যারা সাধক ও বিচারশক্তিসম্পন্ন
তারা সমাজ আর মানুষের কল্যাণেই এই রিপুগুলোকে বশে বা নিয়ন্ত্রণে রাখে। এবং
নিয়ন্ত্রণ রাখাই জরুরি মনে করেন। এদের প্রত্যেকে অনুশাসন করে বিবেক। সেই পরিচালন
করে বোধ, বুদ্ধি বা সঠিক পথের দিশা।
কেউ পুঁথিগত বিদ্যায় পারদর্শী হচ্ছে অথবা মস্ত ডিগ্রিধারী
হচ্ছে কিন্তু তার মাঝে মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়নি। তারাই নানা রকম অসমাজিক কর্মকাণ্ডে
জারিত হচ্ছে । কেননা শুধুমাত্র একডেমিক শিক্ষা মানুষের মনুষ্যত্ব গড়নে ভূমিকা
রাখতে পারে না। এই শিক্ষার উপরেও একজন শিক্ষক সবসময় সঠিক পথে দেখিয়ে চলেছে। তাকে
স্বীকার না করে, তার অনুশীলন অস্বীকার করে তারা রিপু অনুগামী হয়েই থেকে গেছে।
এজন্যই নীতি, আদর্শ, স্বধর্ম, ও শিল্প সাহিত্যের ভূমিকা চরিত্র
গঠনে বা মনুষ্যত্ব বিকাশের
জন্য বিবেকের অনুশাসন সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর। একজন একাডেমিক অশিক্ষিত ব্যক্তিও
যদি রুচিবান হন, শিল্পের বিভিন্ন শাখার চর্চা থাকে, যেমন চলচ্চিত্র, চিত্রকলা, ভাস্কর্য,
এবং সাহিত্যের বিভিন্ন মাধ্যম, যেমন গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা প্রবন্ধ ইত্যাদির
সাথে ঘনিষ্ঠভাবে নিজেকে সম্পৃক্ত করে, প্রাথমিক ভাবে তখন তার ষড়রিপু সে নিয়ন্ত্রণ
করার রসদ তিনি এর মধ্য থেকেই আহরণ করতে সমর্থ হন। এজন্যই শিল্প সাহিত্যের আবর্তে
থাকা মানুষগুলো সচেতন, সামাজিক, স্বশিক্ষিত ও অসাম্প্রদায়িক চেতনাধারী হয়ে থাকেন।
হয়তো এখানে প্রশ্ন থাকতে পারে- পৃথিবীর সব শিল্প কিন্তু আত্মসংযমের শিক্ষা দেয় না।
অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় শিল্প, সাহিত্য, কলা বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিও নিজেকে ভুল
পথে পরিচালিত করে এবং নীতি আদর্শ বর্জিত জীবন-যাপন করে। এক্ষেত্রে আমাদের জন্যে
অতিউত্তম আশ্রয় হল বিবেককে জাগ্রত করা, সম্যকমার্গের চর্চা করা এবং সব বিষয়ে
মাত্রাজ্ঞ হওয়া।
তারপরও পক্ষান্তরে বিচার করলে দেখি- শিল্প সাহিত্য বর্জিত
মানুষগুলোই গোঁয়ার সাম্প্রদায়িক ও কুরুচিসম্পন্ন মনোভাবের অধিকারী হন, তা সে যত বড়
ডিগ্রীধারীই হোন না কেন। যে ধর্মে, যে জাতিতে, যে সমাজে, যে পরিবেশে এ ষড়রিপু
দমনের শিক্ষা পদ্ধতি নেই, সেই ধর্মে সেই সমাজে সেই জাতিতে নানা অশান্তি লেগেই
থাকবে। নানা অপকর্ম লেগেই থাকবে। এই শিক্ষাদান আমরা যার থেকে পেয়ে থাকি তাকেই
আমরা ঘুম পাড়িয়ে রাখি।
তাই সর্বোপরি এই চেতনার অনুগামী হওয়া খুব জরুরি যে চেতনা একজন
মানুষকে বিবেকের অনুগামী হতে সদাসর্বদা নির্দেশ দেয়। যারা নিজেদের মধ্যে বিবেককে
জাগ্রত রেখেছেন তারাই প্রকৃত অর্থে একজন স্বয়ং সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠেছেন। সে
শিল্পী, সাহিত্যিক, ডিগ্রিধারী কিংবা নিরক্ষর যাই হোক না কেন। ভিতরের আলোর
প্রতিফলন হলে তবেই সে সঠিক পথের দিশা দেখতে পায় এবং জ্ঞানের সত্যরূপ উদ্ভাসিত
হয়।
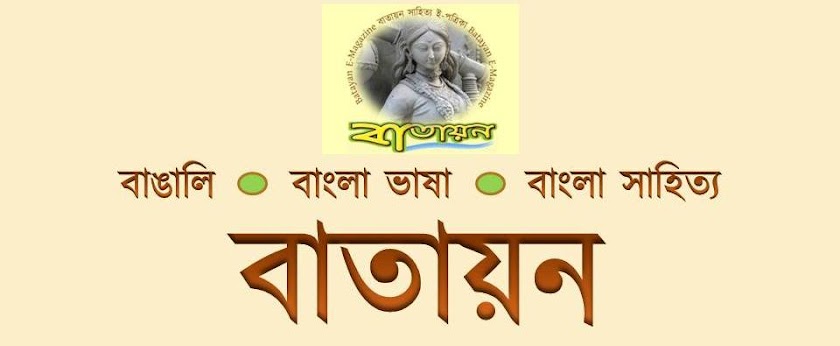















দুটি লেখাই ভালো হয়েছে।
ReplyDeleteঅনেক ধন্যবাদ। পরিচয়টা দেবেন না!
ReplyDelete